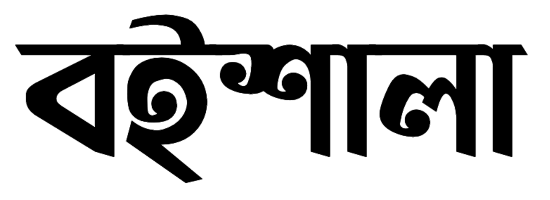১৯২৩ সাল থেকে (বাংলা নাটকে)পালা বদলের যে পরিচয় আমরা পাই-সেই পরিচয়কে…আধুনিক করে তুলেছে গণচেতনার উপলব্ধি ও উপস্থাপনা। আধুনিক চেতনার মেজাজ ও গণচেতনার স্বরূপকে ব্যাখ্যা করেছেন।… মানুষের শ্রেণী-চরিত্রের পরিচয় গণচেতনার প্রসারিত রূপ এই পর্বের নাটকে বাস্তবভিত্তিক চেতনা বা সমাজ স্বরূপকে আরও দৃঢ়ভিত্তিক প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। মন্মথ রায় থেকে বিংশ শতাব্দীর অপরাপর নাটকগুলির মধ্যে লেখক ড. চন্দ্র নাট্যবিচারের মানদণ্ডকে যুক্তিসিদ্ধ এবং ইতিহাস-সম্মতরূপেই বিশ্লেষণ করেছেন। অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর গড়ে ওঠা রাষ্ট্রব্যবস্থা, সমাজ, ধর্মদর্শন, ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র কিভাবে নবতর ভাব পরিমণ্ডল নির্মাণ করেছে এবং তার দ্বারা নাটক কতখানি প্রভাবিত এই মৌলিক মানদণ্ডকে লেখক প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন। প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কালের আবির্ভূত নাট্যকারদের সঙ্গে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এবং স্বাধীনতা কালের নাট্যকারদের মধ্যে দেশকালের স্বাভাবিক ব্যবধান তাঁদের মানসিকতায় এবং শিল্পধর্মে প্রতিফলিত হয়েছে। এই স্বাতন্ত্রকে যথাযযাগ্য মূল্যায়নের কারণে গ্রন্থটিকে দুটি পর্বে ভাগ করে লেখক বিজ্ঞানসম্মত সমাজভাবনার পরিচয় দিয়েছেন-সেই সঙ্গে নাট্যকারদের এবং তাঁদের রচিত নাটকগুলির বিশেষত্ব ব্যাখ্যায় সুষ্ঠু চিন্তারীতি ও বিন্যাস প্রণালীকে উপস্থাপিত করেছেন। ১৯৬০-এর পরবর্তী নাটক জীবনের জটিল গ্রন্থি উন্মােচনে সার্থক হলেও পাশ্চাত্য নাটকের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সেগুলি আন্তর্জাতিক হতে চাইলেও কিভাবে ‘ফর্ম সর্বস্ব হয়ে পড়েছে, উপসংহারে ড. চন্দ্র তাও ব্যাখ্যা করেছেন। লেখক বিষয়ের সীমার মধ্যেও নাট্য সমীক্ষায় সামগ্রিতাকে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন।