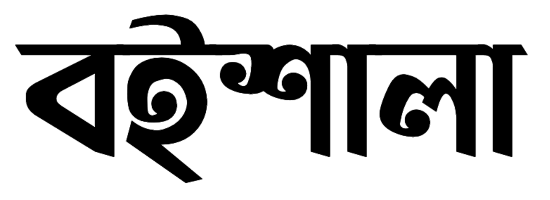“বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য” বইয়ের প্রথম ফ্ল্যাপ এর লেখা:
অন্যতম প্রধান রূপকার সুকুমার সেনের এই মননঋদ্ধ গ্রন্থ নিছক গদ্যসাহিত্যের ইতিহাস বর্ণনা নয়, বাংলা গদ্যের শুরুর শুরু থেকে রবীন্দ্রপর্ব তথা আধুনিক কাল পর্যন্ত বিস্তৃত এক দীর্ঘ পথের পরিক্রমা। ইতিহাস তাে আছেই সেই সঙ্গে বাংলা সাধু ও চলিত গদ্যের অন্তলোকের অনুসন্ধান । লেখক ষােড়শ শতকে পয়ার ছন্দে রচিত কাব্যে বাংলা গদ্যের পদচিহ্ন আবিষ্কার করেছেন। যদিও চিঠিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ এবং প্রয়ােজন ছাড়া বাংলা গদ্যের স্থান সাহিত্যের। প্রাঙ্গণে তখনও সূচিত হয়নি। সপ্তদশ শতকে। পাের্তুগিজ মিশনারি এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে ইংরেজ মিশনারিদের পরিকল্পনায় বাংলা গদ্য কাব্যের খােলস ভেঙে চিন্তা-চেতনার ভাষা, যুক্তির ভাষা হয়ে উঠেছে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয়। বিদ্যালঙ্কার বাংলা গদ্যকে রূপদক্ষ করে। তুলেছিলেন এই পর্বে। লেখক রচনাংশের বিপুল উদাহরণ সহযােগে দেখিয়েছেন কীভাবে বাংলা। গদ্যভাষা প্রথম আভিজাত্য লাভ করেছে। রামমােহনের হাতে। কেন বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্য। সাহিত্যের সৌন্দর্য ও শিল্পপ্রাণের স্রষ্টা ; কোন দিক থেকে প্যারীচাঁদ ও হুতােম চলিত গদ্যের বৈপ্লবিক উদগাতা। ভাষাতত্ত্ব ও তথ্যের উপস্থাপনায় লেখক বিশ্বেষণ করেছেন ‘সৃষ্টির উৎসবে। নির্দ্বন্দ্বভাবে বাংলা গদ্যের’ আসন কীভাবে দৃঢ় হয়েছে বঙ্কিমচন্দ্রের সহায়তায়। সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথ ও সমসাময়িক বহু প্রধান-অপ্রধান। স্রষ্টার গদ্যরচনার নির্ভরযােগ্য আলােচনা । বাংলা গদ্য আজ মননচর্চা ও শিল্পসৃষ্টিতে নিজের শক্তি ও যােগ্যতা প্রমাণ করেছে। আর এই গ্রন্থ ধরে। রেখেছে সেই তিন শতাব্দীর অপরিমেয় ইতিবৃত্ত ও অভিযাত্রার দিনপঞ্জী। দীর্ঘদিন অমুদ্রিত থাকার পর ‘বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্য’-এর পরিবর্ধিত ও সুসম্পাদিত আনন্দ সংস্করণ সাহিত্য-পাঠকদের বহুদিনের অভাব ও প্রত্যাশা পূরণ করল।