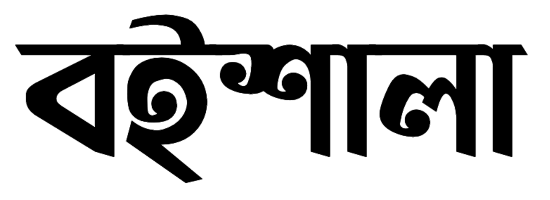পল্লীসমাজ
‘সাত কোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধ জননী,/ রেখেছ বাঙালী ক’রে, মানুষ কর নি/’’ বলে বাঙালি জাতির উপর বিস্তর ক্ষোভ প্রকাশ করলেও, আদতে, বাঙালির প্রকৃত মুখচ্ছবিখানি ততটা নিখুঁতভাবে আঁকতে পারেননি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১—১৯৪১ খ্রি.), যতটা নিপুণভাবে পেরেছিলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬—১৯৩৮ খ্রি.)।
শরৎচন্দ্রের একেকটা গল্প—উপন্যাস যেন গ্রামকেন্দ্রিক বাঙালির গার্হস্থ্যজীবনের একেকটি প্রামাণ্য দলিল। গ্রামবাংলার জীবন এবং সমাজকে রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন outsider —এর অষ্পষ্টতায়, ফলে তা অপূর্ণ ও অগভীর; জসীমউদ্দীনের (১৯০৩—১৯৭৬ খ্রি.) চোখে ছিল সেঁটে—বসা প্রিয়তা—মুগ্ধতার চিরপরিচিত চশমাখানা; ফলে সেই জীবন আরোপিত সৌন্দর্যে beautified; আর জীবনানন্দ দাশের (১৮৯৯—১৯৫৪ খ্রি.) গ্রামীণ জীবন ও প্রকৃতি তো গোটাটাই edited reality, ফলে তা প্রতীকায়িত ও কল্প—চিত্রকল্পময়। — বাংলাদেশের গ্রাম এবং গ্রামের মানুষকে নির্ভেজালভাবে এবং নিখুঁতভাবে অঙ্কনের একক কৃতিত্ব ওই শরৎচন্দ্রেরই।
বাংলাদেশের পল্লীর জীবন ও সমাজ আসলে কেমন, সেটা যদি কোনো অনভিজ্ঞ, অবাঙালি বিশদভাবে জানতে ব্রতী হন, তাহলে তাঁকে পল্লীসমাজ (১৯১৬) পড়তে দিলেই তাঁর কার্যসিদ্ধি হবে। একটিমাত্র উপন্যাস পড়েই তিনি গ্রামবাংলার আবহমান জীবন ও সমাজের সমীকরণ—সূত্রটি পেয়ে যাবেন। যদিও এ উপন্যাসে বিশ শতকের প্রথমার্ধের গ্রামবাংলার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, তবু এ—কথা সংশয়াতীতভাবে সত্য যে, এ উপন্যাস—রচনার শতবর্ষ পেরিয়ে গেলেও ছবিটার তেমন কোনো উনিশ—বিশ হয়নি— রমা, রমেশ, বেণী ঘোষালেরা সেকালে যেমন ছিল, একালেও তেমনই আছেÑ হয়তো নতুন চলনে—বলনে, এই আর কী!