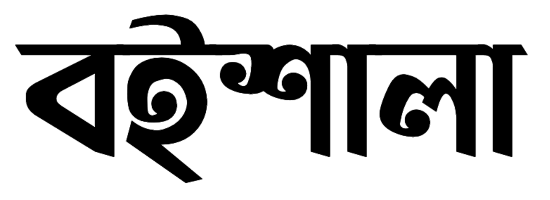হাট-বাজারে আমরা দেখতে পাই, একটা পণ্যের সঙ্গে অন্য একটা পণ্যের বিনিময় ঘটেছে; অথবা একটা বিশেষ পরিমাণ মুদ্রায় একটা বিশেষ পরিমাণ পণ্য বিক্রি হচ্ছে। একে বলে পণ্যের মূল্য রূপ। প্রতিদিনের এই প্রত্যক্ষগোচর ঘটনার পেছনের রহস্য উদঘাটন মার্কসের আগে আর সম্ভব হয়নি। এরিস্টটল এর উত্তর দিতে চেষ্টা করেছিলেন, এডাম স্মিথ এবং রিকার্ডো অনেকটা অগ্রসর হয়েও সফল হননি। এরিস্টটলের পরবর্তী দুই হাজার বছরে বহু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও গবেষণা সম্ভব হয়েছে; কিন্তু পণ্যের মূল্য-রূপটার প্রতিদিনের একটি ক্ষুদ্র বিষয় সম্বন্ধে সত্য আবিষ্কার মার্কসের আগে আর হতে পারেনি। এর কারণ কী? মানুষের গোটা দেহটা সম্বন্ধে বিচার বিশ্লেষণ যত সোজা, এর মূলভিত্তি জীবকোষ সম্পর্কে ধারণা তত সোজা নয়। বৈজ্ঞানিক গবেষণা অপেক্ষা অর্থনৈতিক কাঠামো সম্পর্কে বিচার করাটা আরও কঠিন। এর জন্য যেমন নেই কোনো বিজ্ঞানাগার, তেমনি পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষণের জন্যেও কোনো অনুবীক্ষণ যন্ত্র অথবা রাসায়নিক প্রক্রিয়া নেই। সামাজিক বিষয়ে যে চিন্তাপ্রণালী অবলম্বন করতে হবে তাকে বলা হয় বিয়োজনরীতি (অনংঃৎধপঃরড়হ)। মানুষের শ্রমজাত দ্রব্যের পণ্যরূপ অথবা পণ্যের মূল্য রূপই হলো বুর্জোয়া সমাজের অর্থনৈতিক জীবকোষ। এই জীবকোষ থেকেই আমরা বুর্জোয়া অর্থনৈতিক সমাজ কাঠামোর পরিষ্কার ধারণায় পৌঁছাতে পারি। মার্কসের বিচারের বিষয় হলো পুঁজিতন্ত্রী সমাজের উৎপাদন-প্রথা এবং বিনিময়ব্যবস্থা। মার্কসের সময় আদর্শ পুঁজিতন্ত্রী সমাজ ছিল ইংল্যান্ডে। এই কারণেই মার্কস তার বৈজ্ঞানিক মতবাদ গড়ে তুলতে ইংল্যান্ডকেই সাক্ষ্য ও নিদর্শনরূপে ধরেছেন। পুঁজিবাদী উৎপাদনের প্রভাবে বিশেষ একটি সমাজ শ্রেণি সংঘর্ষের দিকে কতোটা অগ্রসর হয়েছে তা আমরা বিশদভাবে দেখতে চাই না। দেখতে হবে, এই বিশিষ্ট উৎপাদন প্রথার পেছনে যে মূলীভূত সত্য এবং সূত্র রয়েছে তা কী করে অবশ্যম্ভাবীরূপে এবং অপ্রতিরোধ্যভাবে গড়ে এবং ভাঙার কাজ করে চলেছে। যে আধুনিক শিল্পের দিক থেকে বেশি অগ্রসর তার প্রভাব অনগ্রসর অথবা অল্প-অগ্রসর দেশগুলোর উপর পড়বেই। প্রথমোক্ত দেশগুলোতে যা আজ সম্ভব হয়েছে, অনুন্নত দেশগুলোতেও তা অবশ্যই হতে হবে।